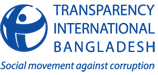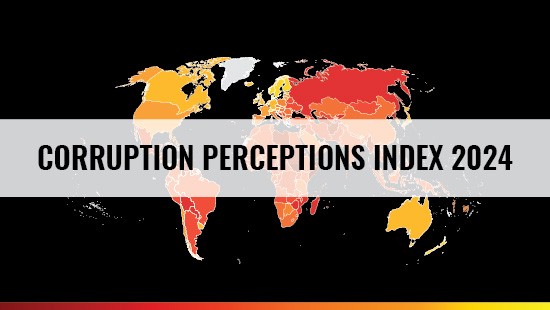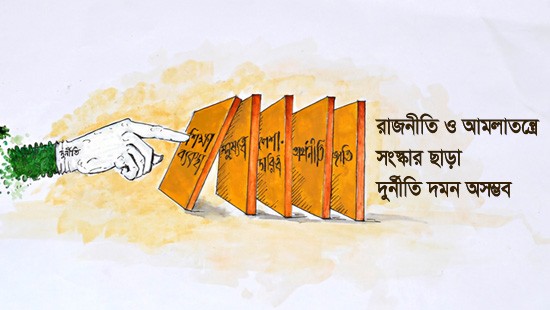প্রকাশকাল: ১০ জানুয়ারি ২০১৩
দুর্নীতির বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন
ইফতেখারুজ্জামান
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটি কার্যকর ও টেকসই সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে ১৯৯৬ সাল থেকে কাজ করছে। টিআইবি এ উদ্দেশ্য অর্জনে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে গবেষণা, নাগরিক সম্পৃক্ততা এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে দুর্নীতিবিরোধী আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রায়োগিক সামর্থ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে জ্ঞানভিত্তিক অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।
এর অংশ হিসেবে টিআইবি গত ২৮ ডিসেম্বর 'সেবা খাতে দুর্নীতি : জাতীয় খানা জরিপ ২০১২' প্রকাশ করেছে।
পদ্মা সেতু প্রকল্প, হলমার্ক, ডেসটিনি, রেলে নিয়োগ, শেয়ারবাজার ইত্যাদির মতো উচ্চ পর্যায়ের দুর্নীতির আগ্রাসী মিছিলে যখন সরকার বিব্রত, মামলার বোঝায় দুদক প্রায়ই কিংকর্তব্যবিমূঢ়, দেশবাসী উদ্বিগ্ন ও হতাশ, আন্তর্জাতিক তুলনামূলক অবস্থানের মাপকাঠিতে যেখানে বাংলাদেশ গতবারের তুলনায় ২৪ ধাপ নিচে, সেইক্ষণে কিঞ্চিৎ আশার আলো দেখিয়েছে এই জরিপ। সার্বিক বিশ্লেষণে জরিপের উত্তরদাতাদের ৬৩.৭ শতাংশ সেবা খাতে কোনো না কোনো দুর্নীতির শিকার হয়েছে। তুলনাযোগ্য মাপকাঠিতে ২০১০-এর জরিপ অনুযায়ী গতবারের ৮৪ শতাংশের স্থলে এবার দুর্নীতির শিকারের হার ৫৫.৮ শতাংশ।
সেবা খাতে এই দুর্নীতি হ্রাস কিছুটা শুভসংকেত হলেও আত্মসন্তুষ্টির খুব সামান্যই অবকাশ রয়েছে। সুশাসন ও মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য অপরিহার্য যে খাতগুলো, বিশেষ করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, ভূমি প্রশাসন, বিচারিক সেবা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও স্থানীয় সরকারের মতো খাতে দুর্নীতির ফলে মানুষের হয়রানির অভিজ্ঞতা এখনো সবচেয়ে বেশি। বিশেষ করে আইনশৃঙ্খলা খাতে উন্নতি খুবই নগণ্য এবং এখনো সর্বোচ্চ উদ্বেগজনক অবস্থায়ই রয়েছে। প্রায় ৭৬ শতাংশ এ খাতে দুর্নীতির শিকার হয়েছে (২০১০-এ ছিল ৭৯.৭ শতাংশ)। বিচারিক সেবা খাতে উন্নতি উল্লেখযোগ্য। গতবারের ৮৮ শতাংশের ক্ষেত্রে এবারের জরিপ অনুযায়ী দুর্নীতির শিকার হওয়া সেবাগ্রহীতার হার ৫৭.১ শতাংশ; যদিও এ হারও নিঃসন্দেহে অত্যন্ত উদ্বেগের কারণ। আরো একটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য খাত হলো ভূমি প্রশাসন। এ ক্ষেত্রেও মানুষের দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার ৫৯ শতাংশ।
তা ছাড়া দুর্নীতির কারণে ক্ষতির পরিমাণ বেড়েছে। খানাপ্রতি ঘুষের হার যেখানে ২০১০-এ ছিল তিন হাজার ১৮৪ টাকা, এবার সেটা ছয় হাজার ৯০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে। যার ফলে সার্বিক হিসাবে জাতীয়ভাবে এ ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২১ হাজার ৯৫৫ কোটি টাকা, যা পদ্মা সেতুর প্রাক্কলিত ব্যয়ের প্রায় সমান। ২০১০-এর প্রাক্কলন অনুযায়ী সেবা খাতে দুর্নীতির জন্য জাতীয় আয়ের ১.৪ শতাংশ ক্ষতি হয়েছিল। এবার তা বেড়ে ২.৪ শতাংশ হয়েছে। অন্যদিকে বার্ষিক জাতীয় বাজেটের হিসাবে ক্ষতির হার বর্তমানে ১৩.৪ শতাংশ, যা ২০১০-এ ৮.৭ ছিল। জরিপের তথ্যে আবারও প্রতীয়মান হয়েছে যে দুর্নীতির নেতিবাচক প্রভাব তুলনামূলকভাবে কম আয়ের মানুষের ওপর বেশি পড়ে। দুর্নীতি হ্রাসের অপরিহার্য পূর্বশর্ত হিসেবে, বিশেষ করে বড় ধরনের দুর্নীতির নিয়ন্ত্রণে যেরূপ দৃষ্টান্ত স্থাপনের প্রয়োজন, সে ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন নেই।
দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনের একজন কর্মী হিসেবে প্রায়ই হতাশার মুখোমুখি হই। আমাদের আন্দোলনের ফলে সারা দেশে সাধারণ মানুষের মধ্যে দুর্নীতিবিষয়ক সচেতনতা ও চাহিদা অনেক বেড়েছে। দুর্নীতি এখন মানুষের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে স্থান পেয়েছে; গণমাধ্যমে এক বিরাট জায়গা করে নিয়েছে দুর্নীতিবিষয়ক সংবাদ, আলোচনা, মন্তব্য। সব রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি এখন দুর্নীতি প্রতিরোধ। প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রিপরিষদের অনেক সদস্য ও জনপ্রতিনিধি এবং সরকারের সর্বস্তরের কর্ণধাররা বক্তৃতা-বিবৃতিতে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলেন। যদিও বাস্তব প্রয়োগ একান্তই হতাশাব্যঞ্জক।
সবচেয়ে কষ্ট হয়, আত্মসম্মানে আঘাত লাগে যখন দুর্নীতির কারণে বিদেশিরা আমাদের সরকারকে জ্ঞানদান শুরু করেন। তাঁদের কারো কারো উদ্দেশ্য মহৎ থাকতে পারে, কারণ বাংলাদেশে অর্থ সাহায্য প্রদানের উৎস যেহেতু তাঁদের দেশের জনগণের করের টাকা, সে জন্য তাঁরাও উদ্বিগ্ন হবেন- এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হই যখন বিশ্বব্যাংকের মতো প্রতিষ্ঠান, কয়েক বছর আগেও যার স্বচ্ছতার ক্ষেত্রে গর্ব করার মতো যুক্তি খুঁজতে হলে বড় ধরনের গবেষণার দরকার হতো, তার কাছ থেকেই বাংলাদেশকে দুর্নীতির অভিযোগের কারণে পদ্মা সেতু প্রকল্পে অর্থ জোগান দেওয়া হবে না- এ রকম হুমকি শুনতে হয়।
তা সত্ত্বেও আমরা আশাবাদী। আশাবাদী এই কারণে যে দেশের সাধারণ মানুষ কখনো ভুল করেনি, যথাসময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে গৌরবময় ইতিহাস রচনা করেছে। দুর্নীতি প্রতিরোধের ক্ষেত্রেও দেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নে সফল হবে। তবে এ সংগ্রাম দীর্ঘমেয়াদি; পাড়ি দিতে হবে অনেক ঘাত-প্রতিঘাত।
টিআইবির কার্যক্রম কোনো সরকার, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নয়; শুধু দুর্নীতির বিরুদ্ধে। আর সে কারণে সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির পরিবেশ সৃষ্টিতে অনেক সময় ক্ষমতাবানদের একাংশের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সত্ত্বেও টিআইবি সব সরকারের সঙ্গেই একযোগে কাজ করে রাষ্ট্রের দুর্নীতিবিরোধী আইনি ও প্রতিষ্ঠানিক অবস্থান সুদৃঢ় করতে সচেষ্ট।
বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় সরকারের সময় টিআইবিকে বন্ধ করে দেওয়া হবে, সারা দেশের ৬৪ জেলায় মামলা করা হবে'- এ রকম হুমকি শুনতে হয়েছে। মহান সংসদেও টিআইবির বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করা হয়েছে। তেমনি সেই সরকারের সময়ই টিআইবি সরকারের সঙ্গে কাজ করে সরকারকে রাজি করাতে পেরেছে দুর্নীতি দমন আইন ২০০৪ প্রণয়ন করতে, যার মূল খসড়াটি টিআইবিরই করা।
একইভাবে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় টিআইবিকে একদিকে যেমন সিডর-পরবর্তী ত্রাণ কার্যক্রমের মতো ক্ষেত্রে দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরার কারণে প্রভাবশালী উপদেষ্টাদের রক্তচক্ষু দেখতে হয়েছে, তেমনি অন্যদিকে জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী আন্তর্জাতিক কনভেনশনের সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে টিআইবি ওই সরকারকেই রাজি করাতে পেরেছে।
চারদলীয় সরকারের সময়ের ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকারের সময়ও সংসদ বর্জন ও কোরাম সংকট এবং সংসদ সদস্যসুলভ কার্যকর ভূমিকা পালনে ঘাটতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য টিআইবিকে বিরাগভাজন হতে হয়েছে। অন্যদিকে টিআইবি তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ ও তথ্য প্রদানকারী সুরক্ষা আইন ২০১১-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়নে সরকারের সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। একইভাবে জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী আন্তর্জাতিক কনভেনশনের বাস্তবায়ন পরিকল্পনা গ্রহণ এবং এর অগ্রগতি পর্যালোচনা সাফল্যের সঙ্গে সম্পাদন, জাতীয় শুদ্ধাচার নীতির খসড়া প্রণয়ন ও দ্বিতীয় প্রজন্মের নাগরিক সনদের মতো সরকারের ইতিবাচক উদ্যোগে টিআইবি সহযোগী হওয়ার সুযোগ পেয়েছে।
চারদলীয় ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মতোই যখন বর্তমান সরকার বাজেটে কালো টাকাকে বৈধতা দেওয়ার মতো অসাংবিধানিক পদক্ষেপ নিয়েছে, তখন টিআইবি সমালোচনায় সোচ্চার থেকেছে। একইভাবে টিআইবি ধারাবাহিকভাবে প্রতিবাদ করে আসছে সরকারি ক্রয় আইনের নেতিবাচক সংশোধনের, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিসহ প্রভাবশালী মহলের টেন্ডারবাজি, দখলবাজি, ভর্তি বাণিজ্য, নিয়োগ বাণিজ্যসহ সব ধরনের ক্ষমতার অপব্যবহার, বিদ্যুৎ খাতের সিদ্ধান্তকে বিশেষ আইনবলে প্রশ্নের ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়া, টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের ক্ষমতা খর্ব করা, পরিবেশের ওপর প্রভাব নিরূপণ না করে রামপালে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন এবং কোনো ধরনের ক্রয়নীতি অনুসরণ না করে সাহারা কম্পানির সঙ্গে আবাসন খাতে ব্যবসার সুযোগ দেওয়ার মতো বহু নেতিবাচক সিদ্ধান্তের। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি মোকাবিলায় সরকারি ও বিদেশি অর্থ সহায়তায় সৃষ্ট তহবিলের পরিচালনায় স্বচ্ছতা ও প্রকল্প বাস্তবায়নে জবাবদিহির চাহিদা সৃষ্টিতে সোচ্চার হওয়ার কারণে প্রভাবশালী মহলের বিরাগভাজন হতে হয়েছে টিআইবিকে।
অন্যদিকে দুর্নীতি দমন আইনের কিছু সংশোধনীর প্রস্তাব করে সরকার তার নির্বাচনী অঙ্গীকারের পরিপন্থী যে অবস্থান গ্রহণ করেছিল, তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ত করে টিআইবি সক্ষম হয়েছে ওই অবস্থান থেকে সরকারকে সরিয়ে আনতে। যদিও সরকারের এ উদ্যোগের ফলে দুর্নীতি দমন কমিশনের ওপর এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক চাপ সৃষ্টি হয়েছে এবং কমিশনের গতিশীলতায় ঘাটতি ঘটেছে, যা নিয়ে টিআইবি সোচ্চার থেকেছে। টিআইবির কাজের মূল প্রেরণা আমাদের গৌরবময়
ইতিহাস, বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণ-আন্দোলন, আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ, স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন। গণতন্ত্রের জন্য, সব মানুষের সমান অধিকারের জন্য, একটি সুশাসিত সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য এ দেশের মানুষের অকাতরে রক্ত দেওয়ার যে ঐতিহ্য, তার বাহক হিসেবে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আমাদের প্রিয় স্বাধীনতার স্বপ্নপূরণে অন্যতম অন্তরায় যে দুর্নীতি, তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো এ দেশের প্রতিটি মানুষের মৌলিক দায়িত্ব ও অধিকার। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, দুর্নীতি একুশের চেতনার পরিপন্থী; দুর্নীতি স্বাধীনতার চেতনার সঙ্গে সাংঘর্ষিক; স্বাধীনতার স্বপ্নপূরণে আমরা চাই সুশাসিত দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ।
তবে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে কোনো ম্যাজিক বুলেট আছে বলে জানা নেই, যদি থাকে তা দেশের দুই নেত্রীর হাতে থাকতে পারে। যদিও অলীক মনে হতে পারে, আশা করতে দোষ নেই যে তাঁরা দুজনই একদিন উপলব্ধি করবেন, যথেষ্ট হয়েছে, শত বিভেদ সত্ত্বেও দুজন একমত হয়ে দেশবাসীর কাছে অঙ্গীকার করবেন, দুর্নীতিকে আর প্রশ্রয় দেব না, সে যে-ই হোক, প্রিয়জন থেকে শুরু করে মন্ত্রী, জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের দলীয় নেতারা- সবার জন্য সমভাবে প্রযোজ্য হবে এই অঙ্গীকার।
দুই নেত্রীই তো পারেন এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করতে, যেখানে সংসদ বয়কটের রাজনীতির পরিবর্তে এমন একটা সংসদ আমরা পাব, যার কাছে সরকার জবাবদিহি করতে বাধ্য হবে। এমন একটা প্রশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে, যেখানে দলীয় রাজনৈতিক প্রভাব থাকবে না। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো এমনভাবে কাজ করবে, যেখানে দলীয় বা অন্য কোনো পরিচয় কোনো বিবেচ্য বিষয় হবে না; বিচারব্যবস্থায় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলিতে দলীয় বিবেচনা নয়, শুধু পেশাগত উৎকর্ষই মাপকাঠি হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে; দুর্নীতি দমন কমিশনকে নখদন্তহীন বাঘে পরিণত করার অপচেষ্টা বন্ধ হবে।
প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রীপরিষদের সদস্য, সংসদ সদস্য, সব জনপ্রতিনিধি, তাঁদের পরিবার-পরিজনসহ ক্ষমতাবানদের সম্পদের সঠিক বিবরণ প্রকাশ শুধু ফাঁকা বুলি থাকবে না; অনুপার্জিত আয় ও কালো টাকা বৈধ করার রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধ হবে; ঋণখেলাপি, টেন্ডারবাজি, টোলবাজি, পেশিশক্তি, ভূমিদস্যুতা ও কালো টাকার প্রভাবে রাজনৈতিক অঙ্গন কলুষিত হবে না, শেয়ারবাজারও তাদের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি পাবে; সরকারি ক্রয় খাতে ক্ষমতার অপব্যবহার ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব বন্ধ হবে।
তবে দুই নেত্রী তথা রাজনৈতিক দল, জনপ্রতিনিধি, সরকার ও সরকারের ভেতরে ও বাইরে গণতন্ত্রের মৌলিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রত্যাশিত ভূমিকা কিভাবে ও কত শিগগির অর্জিত হবে তা নির্ভর করবে জনগণের ওপর। জনগণই চাইবে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠানগুলো কার্যকর হোক: জনগণই চাইবে দুর্নীতি যারা করে তারা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ভোগ করুক; জনগণই চাইবে রাজনৈতিক অঙ্গীকার বাস্তবায়িত হোক কারো প্রতি ভয় বা করুণা না করে; জনগণই চাইবে নেতা-নেত্রীদের আচরণে গণতান্ত্রিক চর্চার প্রতিফলন ঘটুক, দেশের স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া হোক ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে। জনগণের এই চাওয়া, এই দাবি যত বেশি জোরালো হবে, দুর্নীতি প্রতিরোধ ততটাই ত্বরান্বিত হবে। ক্ষমতার উৎস যে জনগণ, তা যেন সরকার ও জনগণ ভুলে না যায়। এর জন্য গবেষণালব্ধ তথ্য ও বিশ্লেষণভিত্তিক প্রচারণা ও চাহিদা জোরদার করার সামাজিক আন্দোলনটি টিআইবিকে করে যেতে হবে এমন একটা সময় পর্যন্ত, যখন দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা যাঁদের হাতে তাঁরা তাঁদের যথাযথ ভূমিকা কার্যকরভাবে পালন করবেন।
লেখক : নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি
লেখাটি ১০ জানুয়ারি, ২০১৩ দৈনিক ![]() তে প্রকাশিত হয়েছে।
তে প্রকাশিত হয়েছে।