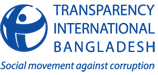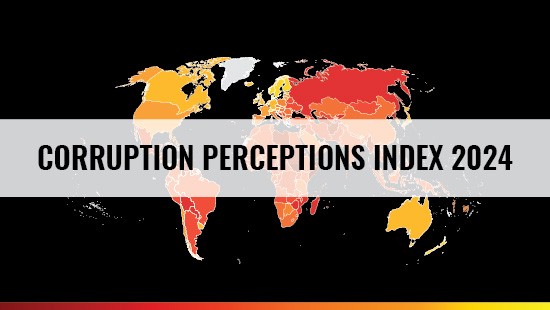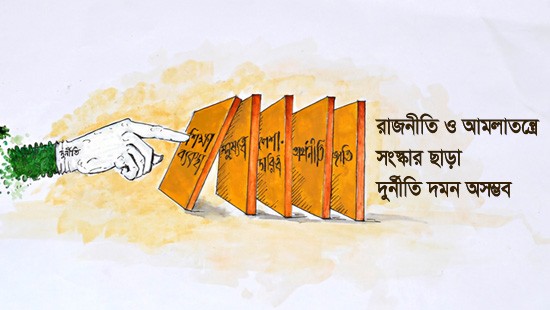প্রকাশকাল: ২৯ ডিসেম্বর ২০১২
সেবা খাতে দুর্নীতি
হতাশায় আশার আলো—এরপর কী
 পদ্মা সেতু প্রকল্প, হল-মার্ক, ডেসটিনি, রেলে নিয়োগ, শেয়ারবাজার ইত্যাদির মতো উচ্চপর্যায়ের দুর্নীতির আগ্রাসী মিছিলে যখন সরকার বিব্রত, মামলার বোঝায় দুদক প্রায়ই কিংকর্তব্যবিমূঢ়, দেশবাসী উদ্বিগ্ন ও হতাশ, আন্তর্জাতিক তুলনামূলক অবস্থানের মাপকাঠিতে যেখানে বাংলাদেশ গতবারের তুলনায় ২৪ ধাপ নিচে, সেই ক্ষণে কিঞ্চিৎ আশার আলো দেখাচ্ছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) কর্তৃক গতকাল ২৮ ডিসেম্বর প্রকাশিত ‘সেবা খাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ ২০১২’। সার্বিক বিশ্লেষণে এই জরিপের উত্তরদাতাদের ৬৩ দশমিক ৭ শতাংশ সেবা খাতে কোনো না কোনো দুর্নীতির শিকার হয়েছেন। তুলনাযোগ্য মাপকাঠিতে ২০১০ সালের জরিপ অনুযায়ী গতবারের ৮৪ শতাংশের স্থলে এবার দুর্নীতির শিকারের হার ৫৫ দশমিক ৮ শতাংশ।
পদ্মা সেতু প্রকল্প, হল-মার্ক, ডেসটিনি, রেলে নিয়োগ, শেয়ারবাজার ইত্যাদির মতো উচ্চপর্যায়ের দুর্নীতির আগ্রাসী মিছিলে যখন সরকার বিব্রত, মামলার বোঝায় দুদক প্রায়ই কিংকর্তব্যবিমূঢ়, দেশবাসী উদ্বিগ্ন ও হতাশ, আন্তর্জাতিক তুলনামূলক অবস্থানের মাপকাঠিতে যেখানে বাংলাদেশ গতবারের তুলনায় ২৪ ধাপ নিচে, সেই ক্ষণে কিঞ্চিৎ আশার আলো দেখাচ্ছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) কর্তৃক গতকাল ২৮ ডিসেম্বর প্রকাশিত ‘সেবা খাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ ২০১২’। সার্বিক বিশ্লেষণে এই জরিপের উত্তরদাতাদের ৬৩ দশমিক ৭ শতাংশ সেবা খাতে কোনো না কোনো দুর্নীতির শিকার হয়েছেন। তুলনাযোগ্য মাপকাঠিতে ২০১০ সালের জরিপ অনুযায়ী গতবারের ৮৪ শতাংশের স্থলে এবার দুর্নীতির শিকারের হার ৫৫ দশমিক ৮ শতাংশ।
অন্যদিকে দৈনন্দিন জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোতে দুর্নীতির মাত্রা এখনো উদ্বেগজনক অবস্থায় রয়েছে। তা ছাড়া দুর্নীতির কারণে ক্ষতির পরিমাণ বেড়েছে। ২০১০ সালের প্রাক্কলন অনুযায়ী সেবা খাতে দুর্নীতির জন্য জাতীয় আয়ের ১ দশমিক ৪ শতাংশ ক্ষতি হয়েছিল, এবার তা বেড়ে ২ দশমিক ৪ শতাংশ হয়েছে। অন্যদিকে বার্ষিক জাতীয় বাজেটের হিসাবে ক্ষতির হার বর্তমানে ১৩ দশমিক ৪ শতাংশ, যা ২০১০-এ ৮ দশমিক ৭ ছিল। জরিপের তথ্যে আবারও প্রতীয়মান হয়েছে যে দুর্নীতির নেতিবাচক প্রভাব তুলনামূলকভাবে কম আয়ের মানুষের ওপর বেশি পড়ে।
সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সেবা খাতে দুর্নীতির প্রকৃতি ও মাত্রা নিরূপণের জন্য প্রতি দুই বছর পর সেবা খাতে দুর্নীতিবিষয়ক জাতীয় খানা জরিপ পরিচালিত হয়। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের বার্লিনভিত্তিক সচিবালয় কর্তৃক প্রকাশিত দুর্নীতির ধারণাসূচক যা করাপশন পারসেপশন ইনডেক্স বা সিপিআই নামে পরিচিত, এর সঙ্গে এই খানা জরিপের কোনো সম্পর্ক নেই। সিপিআই মূলত জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে দুর্নীতির ব্যাপকতার ধারণার একটি আন্তর্জাতিক তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরে। অন্যদিকে এই খানা জরিপ কোনো প্রকার ধারণা বা মতামতনির্ভর নয়, বরং এতে উত্তরদাতাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যের ওপর নির্ভর করে নির্ধারিত খাতে সেবাগ্রহীতা ঘুষসহ যে ধরনের দুর্নীতি বা অনিয়মের শিকার হন, তার চিত্র তুলে ধরা হয়।
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সমন্বিত বহুমুখী নমুনায়ন কাঠামো অনুসরণ করে দৈবচয়ন পদ্বতিতে নমুনায়িত দেশের সাতটি বিভাগের ৬৪টি জেলার মোট সাত হাজার ৫৫৪ খানার অংশগ্রহণে এবারের জরিপটি পরিচালিত হয়েছে। জরিপের পদ্ধতি ও গুণগত উৎকর্ষ নিশ্চিত করতে টিআইবি ছয় সদস্যের বিশেষজ্ঞ প্যানেলের পরামর্শ ও পর্যবেক্ষণে কাজ করেছে। উল্লেখ্য, এবারের জরিপের তথ্যের বিশ্লেষণে ৯৫ শতাংশ নির্ভরযোগ্যতার মাত্রায় সহনশীল বিচ্যুতির সীমা +/- ৪, যা ফলাফলের সর্বোচ্চ যথার্থতার ইঙ্গিত বহন করে।
জরিপে অন্তর্ভুক্ত সরকারি ও বেসরকারি খাতগুলোর মধ্যে শ্রম অভিবাসন এবার সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত (৭৭%); এর পরই রয়েছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা (৭৫.৮%), ভূমি প্রশাসন (৫৯%), বিচারিক সেবা (৫৭.১%), স্বাস্থ্য (৪০.২%), শিক্ষা (৪০.১%) ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (৩০.৯%)। ভৌগোলিক অবস্থানভেদে দুর্নীতির মাত্রা গ্রামাঞ্চলে বেশি, যা এ সমস্যার গভীরতা ও ব্যাপকতার উদ্বেগজনক দৃষ্টান্ত।
শ্রম অভিবাসন খাতে সেবাগ্রহীতারা একদিকে যেমন অন্য সব খাতের তুলনায় বেশি দুর্নীতির শিকার হয়েছেন, তেমনি এ খাতে একটি উল্লেখযোগ্য দিক এই যে যাদের কাছে দুর্নীতির শিকার হতে হয়েছে, তাদের বিরাট অংশ সেবাগ্রহীতার আত্মীয়, প্রতিবেশী বা অন্যভাবে পরিচিত জন। বিষয়টি উদ্বেগজনক এই অর্থে যে দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিক বিস্তারের পাশাপাশি এটি ব্যক্তিপর্যায়ের মূল্যবোধের অবক্ষয়ের উদাহরণ।
সেবা খাতে আদায়কৃত ঘুষের পরিমাপের ভিত্তিতে প্রাক্কলিত হিসাব অনুযায়ী জাতীয়ভাবে বছরে প্রায় ২১ হাজার ৯৫৫ কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে, যা ২০১১-১২ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটের ১৩ দশমিক ৪% এবং জিডিপির ২ দশমিক ৪%। ঘুষ ও নিয়মবহির্ভূত অর্থের পেছনে খানাপ্রতি বার্ষিক গড় ব্যয়ের ৪ দশমিক ৮% খরচ হয়, তবে নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য দুর্নীতির প্রভাব তুলনামূলকভাবে বেশি (মোট ব্যয়ের ৫ দশমিক ৫%)। পক্ষান্তরে ধনীদের ক্ষেত্রে তা তুলনামূলক কম (১.৩%)। অর্থাৎ দুর্নীতির এই বিপুল ক্ষতির বোঝা আপেক্ষিক অর্থে দরিদ্র জনগণের ওপরই বেশি। অন্যদিকে আয়-ব্যয়ের শ্রেণীভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়ার মাপকাঠিতে দেখা যায়, আয়-ব্যয় যত বাড়ে, তত বেশি মানুষ সেবা খাতে দুর্নীতির শিকার হন। এর কারণ হিসেবে দেখা যায়, আয়-ব্যয় যত বৃদ্ধি হয়, তত বেশি খাতে সেবা গ্রহণের সুযোগ বা চাহিদা সৃষ্টি হয়। তা ছাড়া যাদের আয়-ব্যয় বেশি, তাদের ক্ষেত্রে দুর্নীতির মুখোমুখি অবস্থায় অবৈধ লেনদেনের মাধ্যমে সেবা গ্রহণের প্রবণতাও বাড়তে পারে।
তবে আশার কথা, ২০১০ সালের তুলনায় এবারের জরিপের প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী সার্বিকভাবে দুর্নীতি কমেছে দেখা যায়। খাতওয়ারি বিবেচনায়ও স্বাস্থ্য এবং ‘অন্যান্য’ তালিকাভুক্ত খাত যেমন বিআরটিএ, ওয়াসা, পাসপোর্ট, সরকারি খাতে নিয়োগ, বিটিসিএল ও ডাক ছাড়া আর সব গুরুত্বপূর্ণ খাতেই দুর্নীতির ব্যাপকতার হার কমেছে। যেসব খাতে দুর্নীতির ব্যাপকতা কমবেশি নিম্নমুখী, তার মধ্যে রয়েছে: আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, ভূমি প্রশাসন, বিচারিক সেবা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, কৃষি, বিদ্যুৎ, কর ও শুল্ক, শিক্ষা, ব্যাংকিং, বিমা ও এনজিও।
যেসব কারণে সেবা খাতে দুর্নীতির মাত্রা কমেছে বলে অনুমান করা যায়, তার মধ্যে রয়েছে সীমিতভাবে হলেও স্থানীয় পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইনের প্রচারণা ও প্রয়োগের ইতিবাচক প্রভাব; নাগরিক সনদ প্রচলনের ফলে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির সুযোগ সৃষ্টি; ইউনিয়ন পরিষদভিত্তিক ই-তথ্য সেবাসহ কোনো কোনো সেবা খাতে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার; সরকারি কর্মকর্তাদের দুর্নীতিবিরোধী প্রশিক্ষণ; স্থানীয় সরকার পর্যায়ে কোনো কোনো জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্বশীল ভূমিকা; এবং নাগরিক সমাজ, এনজিও ও গণমাধ্যমে দুর্নীতিবিরোধী সক্রিয় প্রচারণার ফলে জনসচেতনতা ও দুর্নীতিবিরোধী অবস্থান।
তবে এসব উদ্যোগের সঙ্গে সেবা খাতের দুর্নীতির ব্যাপকতা হ্রাসের কার্যকারণগত সম্পর্ক রয়েছে কি না, অথবা এই ফলাফল সুনির্দিষ্ট ধারার লঙ্ঘন কি না, তা সঠিকভাবে বলা যাবে না। তদুপরি আত্মসন্তুষ্টির খুব সামান্যই অবকাশ রয়েছে। লক্ষণীয় যে সুশাসন ও মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য অপরিহার্য যে খাতগুলো, বিশেষ করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, ভূমি প্রশাসন, বিচারিক সেবা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও স্থানীয় সরকারের মতো খাতে দুর্নীতির ফলে মানুষের হয়রানি এখনো সবচেয়ে বেশি। বিশেষ করে আইনশৃঙ্খলা খাতে উন্নতি খুবই নগণ্য এবং এখনো সর্বোচ্চ উদ্বেগজনক অবস্থায়ই রয়েছে। প্রায় ৭৫ দশমিক ৮ শতাংশ উত্তরদাতা এ খাতে দুর্নীতির শিকার হয়েছেন, যা ২০১০ সালে ছিল ৭৯ দশমিক ৭ শতাংশ। বিচারিক সেবা খাতে উন্নতি উল্লেখযোগ্য। গতবার এ খাতে দুর্নীতির হার যেখানে ৮৮ শতাংশ ছিল, এবার তা কমে ৫৭ দশমিক ১ শতাংশ হয়েছে; যদিও এই হারও অতীব উদ্বেগের কারণ।
ব্যষ্টিক পর্যায়ে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে দুর্নীতি হ্রাসের এই দৃষ্টান্তকে এগিয়ে নিতে আইনের বাস্তব, প্রভাবমুক্ত ও কঠোর প্রয়োগসহ সব পর্যায়ে গণতান্ত্রিক জবাবদিহি প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন পদক্ষেপকে অব্যাহতভাবে এগিয়ে নিতে হবে। অন্যদিকে দুর্নীতি হ্রাসের অপরিহার্য পূর্বশর্ত হিসেবে, বিশেষ করে বড় ধরনের দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে যেরূপ দৃষ্টান্ত স্থাপনের প্রয়োজন, সে ক্ষেত্রে আমরা অনেক পিছিয়ে রয়েছি। দুর্নীতি যে পর্যায়েই হোক আর এর সঙ্গে সম্পৃক্ততা যারাই থাকুক না কেন, কারও প্রতি করুণা বা ভয় না করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা না হলে দুর্নীতি প্রতিরোধে অগ্রগতি অর্জন এবং তা ধরে রাখা অসম্ভব হবে।
এবারের খানা জরিপের যতটুকু ইতিবাচক ফল, তার ওপর ভিত্তি করে সৃষ্ট সম্ভাবনাকে ধারণ করে আমরা আশাবাদের সঙ্গে এগিয়ে যেতে চাই। আর এই যাত্রাপথে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১৯৭৫-এর স্বাধীনতা দিবসে প্রদত্ত ভাষণ থেকে নিচের উদ্ধৃতিটুকু স্মরণ করি:
‘আমি বলেছিলাম, ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো...আজকে আমি বলব বাংলার জনগণকে—এক নম্বর কাজ হবে, দুর্নীতিবাজদের বাংলার মাটি থেকে উৎখাত করতে হবে। আইন চালাব। ক্ষমা করব না। যাকে পাব, ছাড়ব না। একটা কাজ আপনাদের করতে হবে। গণ-আন্দোলন করতে হবে...এমন আন্দোলন করতে হবে, যে ঘুষখোর, যে দুর্নীতিবাজ, যে মুনাফাখোর...তাদের সামাজিকভাবে বয়কট করতে হবে।...আন্দোলন করতে পারে কে? ছাত্র ভাইয়েরা পারে? পারে কে? যুবক ভাইয়েরা পারে। পারে কে? বুদ্ধিজীবীরা পারে। পারে কে? জনগণ পারে। আপনারা সংঘবদ্ধ হন। ঘরে ঘরে আপনাদের দুর্গ গড়তে হবে। সে দুর্গ গড়তে হবে দুর্নীতিবাজদের খতম করবার জন্য, বাংলাদেশের দুঃখী মানুষের দুঃখ মোচন করবার জন্য...’
চারটি বিষয়ের ওপর তিনি জোর দিয়েছেন: (ক) দুর্নীতিবিরোধী আইন প্রণয়ন ও কার্যকর প্রয়োগ করতে হবে; (খ) অপরাধীকে ছাড় দেওয়া যাবে না, সে যে-ই হোক না কেন; (গ) আইনের প্রয়োগের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সুদৃঢ় করতে হবে এবং (ঘ) দুর্নীতিবিরোধী গণ-আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, জনতার শক্তিতে নির্ভর করে সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে তিনি তরুণ সমাজের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন।
সম্ভবত কাকতালীয় হলেও এটি ঠিক যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ২০০৮ সালের নির্বাচনী অঙ্গীকারে উল্লিখিত কৌশলের অনেকটারই প্রতিফলন ঘটেছিল। তারা দুর্নীতি প্রতিরোধকে শীর্ষ পাঁচটি প্রাধান্যের একটি হিসেবে চিহ্নিত করে। বিরোধী দলের নির্বাচনী অঙ্গীকারেও দুর্নীতির বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান ঘোষিত হয়, যেমনটি কমবেশি দেখা যায় উভয় জোটের প্রায় সব কটি দলেরই নির্বাচনী ইশতেহারে।
আমরা সাধারণ মানুষ যেভাবে দুর্নীতিকে নিয়ন্ত্রিত হতে দেখতে চাই, আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বের বক্তব্যেও তারই যখন প্রতিফলন ঘটতে দেখি, তখন আশান্বিত হই। তবে এই আশাবাদ হতাশায় রূপান্তর হতে দেখি প্রতিনিয়ত। আমাদের প্রিয় স্বদেশের ইতিহাসও তাই বলে। জনগণের ত্যাগের বিনিময়ে, আন্দোলনের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্জনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব যাঁরা গ্রহণ করেন, তাঁদের ব্যর্থতার বোঝা আবার জনগণকেই বইতে হয়। আর তাই জনগণকেই সোচ্চার হতে হয়। জনগণের, বিশেষ করে তরুণ সমাজের দাবি যত জোরদার হবে, দুর্নীতি প্রতিরোধ ততটাই ত্বরান্বিত হবে।
ইফতেখারুজ্জামান: নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)।
লেখাটি ২৯ ডিসেম্বর, ২০১২ দৈনিক তে প্রকাশিত হয়েছে