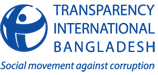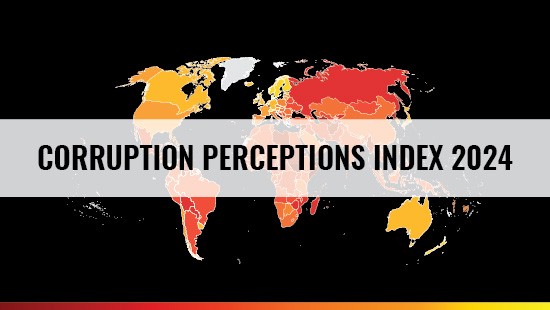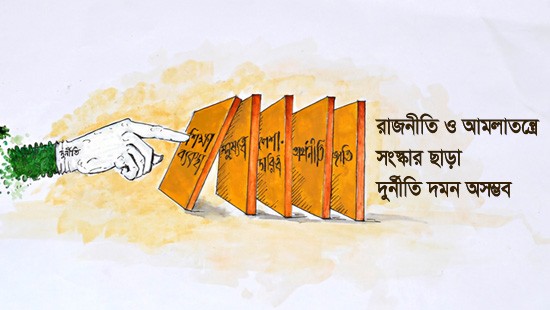প্রকাশকাল: ২২ ডিসেম্বর ২০১২
টিআইবির এমপি সমীক্ষা : পদ্ধতিগত বিতর্ক
এম রফিক হাসান
টিআইবি কর্তৃক জাতীয় সংসদ সদস্যদের কার্যক্রমের ওপর একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পর এ নিয়ে সারা দেশে নানা তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনা-সমালোচনা অব্যাহত রয়েছে। যে কয়েকটি মুখ্য সমালোচনা এ প্রতিবেদন সম্পর্কে তোলা হয়েছে, সেগুলোর অন্যতম একটি হলো_ গবেষণাটির পদ্ধতি নিয়ে। বলা হয়েছে, মহান জাতীয় সংসদের সদস্যদের নিয়ে এ গবেষণা যথাযথ পদ্ধতি অবলম্বন করে করা হয়নি এবং বাস্তবতার সঙ্গে এ গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলের কোনো মিল নেই। বস্তুত তথ্য মন্ত্রণালয়ের বক্তব্য অনুযায়ী এ গবেষণার ফলাফল পূর্বচয়িত এবং প্রশ্নের মাধ্যমে আগের ধারণাকে তুলে এনে গবেষণা বলে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই গবেষণার পদ্ধতিগত দিক সম্পর্কে টিআইবির পক্ষ থেকে কিছু বলার তাগিদ থেকেই এ প্রবন্ধের অবতারণা।
প্রথমে সংক্ষেপে বলা প্রয়োজন, এ গবেষণায় মাঠপর্যায়ে ১৪৯ সংসদ সদস্য সম্পর্কে তথ্য নিয়ে জানা যায় যে, তাদের মধ্যে ৮০ জন সদস্য বিভিন্ন ধরনের ইতিবাচক কাজের সঙ্গে জড়িত। এই ইতিবাচক কাজের তালিকাটি দীর্ঘ এবং রীতিমতো আগ্রহ-উদ্দীপক, যেমন নতুন অবকাঠামো নির্মাণ, ভূমি বরাদ্দ/অনুদান বরাদ্দ প্রাপ্তিতে ভূমিকা রাখা, নতুন চিকিৎসা সেবা সম্প্রসারণ, এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন কোর্স চালু, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ, রাস্তা, সেতু নির্মাণ ও সংস্কার, বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়ন, রেল-সড়ক উন্নয়ন, জলদস্যু নিয়ন্ত্রণ, লবণাক্ততা দূরীকরণ, নদীভাঙন রোধ, পরিবেশ রক্ষা, পাটকল চালুকরণ, চরমপন্থি নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সৃষ্টিতে অবদান, হাওর এলাকায় ডুবন্ত রাস্তা তৈরির উদ্যোগ, এলাকায় বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ, চরাঞ্চলে চিকিৎসাসেবা সম্প্রসারণ, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন, বিরোধীদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখা ইত্যাদি। ১৪৯ সংসদ সদস্যের মধ্যে ৮০ জন অর্থাৎ প্রায় ৫৪ শতাংশ এ ধরনের ইতিবাচক কাজে নিয়োজিত। কোনো কোনো সমালোচক এ পর্যায়ে প্রশ্ন তুলেছেন, বাকি ৪৬ শতাংশ কি শয্যাশায়ী বা অতিশয় অসুস্থ? তারা কি এলাকার দুস্থ, সাহায্যপ্রার্থী, দীন-দুঃখীদের সহায়তা করেন না এবং মানবিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত নেই? এ কথা অবিশ্বাস্য। বাংলাদেশের যে কোনো ওয়াকিবহাল নাগরিকই বলবেন, একজন সংসদ সদস্য প্রায় প্রতিদিনই তার এলাকার সাহায্য-সহায়তাপ্রার্থী লোকদের সাক্ষাৎ প্রদান করেন এবং সাধ্যমতো সাহায্য-সহায়তাও নিশ্চয়ই করে থাকেন। পূর্ববর্তী নির্বাচনের ভূমিকা স্মরণ করেই হোক অথবা পরবর্তী নির্বাচনের কথা বিবেচনা করেই হোক, যারা ব্যক্তিগতভাবে তার সঙ্গে সাহায্যপ্রার্থী হিসেবে দেখা করেন, তাদের সম্ভবমত সাহায্য-সহযোগিতা করা বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতাদের একটি ঐতিহ্যও বটে। কিন্তু টিআইবি গবেষণায় ব্যক্তিপর্যায়ের এসব দান ও সহযোগিতামূলক কার্যক্রমকে বিবেচনা করা হয়নি বরং কেবল সংসদ সদস্য হিসেবে এলাকার উন্নয়নের জন্য যেসব ভূমিকা তারা রেখেছেন সেগুলোই গণ্য করা হয়েছে।
মাঠপর্যায়ে তথ্যদাতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ১৪৯ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে ১৪৪ জন (অর্থাৎ প্রায় ৯৭ শতাংশ) কোনো না কোনো ধরনের নেতিবাচক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত বলেও জানা যায়। এই নেতিবাচক কর্মকাণ্ডও অনুরূপভাবে একজন সংসদ সদস্য হিসেবে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে কৃত এবং এর সঙ্গে এলাকায় উপস্থিতির সরাসরি সম্পর্ক নেই। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই এসব কর্মকাণ্ড সংগঠিত হয়েছে সংসদ সদস্যের দলীয় বা আশ্রয়-প্রশ্রয়প্রাপ্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে এবং তাদের মদদে। লক্ষণীয় টিআইবি গবেষণা প্রবন্ধে এ কথাও বলা হয়েছে, একজন সংসদ সদস্য, যিনি মূলত আইন প্রণয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সংসদ সদস্যদের ভেতরে-বাইরে ব্যাপৃত থাকার কথা, তিনি যে এ ধরনের কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকছেন এর সম্ভাব্য কারণসমূহের অন্যতম হলো_ এলাকায় নিজের দল ও আস্থাভাজন লোকদের জন্য, অন্যায়ভাবে হলেও সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করে দেওয়া, পূর্ববর্তী নির্বাচনে তাদের ভূমিকা এবং আগামী নির্বাচনে তাদের সম্ভাব্য ভূমিকার কথা বিবেচনা করে। নেতিবাচক কাজের তালিকাটিও ইতিবাচক কাজের তালিকার মতোই দীর্ঘ, যা ইতোমধ্যে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে বিধায় এ প্রবন্ধের স্থানাভাবের কথা বিবেচনা করে পুনোরুল্লেখ করা হলো না।
মাঠপর্যায়ে তথ্যসংগ্রহের আগে প্রায় চার বছর ধরে (২০০৯-২০১২) জাতীয় পর্যায়ের পাঁচটি সংবাদপত্র স্ক্যান করে ১৮১ জন সংসদ সদস্য সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের নেতিবাচক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকার প্রতিবেদন পাওয়া যায়। লক্ষ্য করা গেছে, খুব স্বল্পসংখ্যক সংসদ সদস্যই প্রকাশিত নেতিবাচক সংবাদ সম্পর্কে প্রতিবাদ (রিজয়েন্ডার) প্রেরণ করেছেন অথবা আদালতে মানহানির মামলা বা প্রেস কাউন্সিলে মামলার মতো পদক্ষেপ নিয়েছেন। কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন, কেন নির্দিষ্ট ওই পাঁচটি সংবাদপত্রই নেওয়া হলো? কেন অন্য সংবাদপত্র যেগুলো প্রচারসংখ্যা বা পাঠক সংখ্যার দিক থেকে সমপর্যায়ের, এমনকি বেশি, সেগুলো নেওয়া হলো না? গবেষণার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এ সম্পর্কে বলা যায়, একটি গবেষণার পরিসরে সব সংবাদপত্র অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনও পড়ে না, আবার সময় ও সম্পদের সীমাবদ্ধতার কথা বিবেচনা করে এটা সম্ভবও হয় না। বর্তমান গবেষণায় পাঠক সংখ্যা, প্রচার সংখ্যা এবং পাঠকের আস্থাশীলতার কথা বিবেচনা করে মূলধারার জাতীয় পত্রিকাগুলোর মধ্য থেকে পাঁচটিকে বেছে নেওয়া হয়। এর বাইরেও অনেক পত্রিকা ছিল যেগুলো প্রচার সংখ্যার দিক থেকে হয়তো সমান বা বেশি কিন্তু জাতীয় পর্যায়ের পাঁচটি পত্রিকা বেছে নেওয়ার পর আরও অধিকসংখ্যক পত্রিকা অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা অন্তত গবেষণার দিক থেকে থাকে না। সংবাদের বস্তুনিষ্ঠতার সম্ভাবনা বিবেচনায় রেখে স্থানীয় সংবাদপত্রগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। প্রশ্ন তোলা হয়েছে টিআইবি সংবাদপত্রকে কেন তথ্যের উৎস হিসেবে বেছে নিয়েছে? কেন 'পূর্ববর্তী গবেষণা বা আর্কাইভাল উপাত্ত' গণ্য করা হলো না? আমাদের জানা মতে, সংসদ সদস্যদের নিয়ে এটি দেশে প্রথম এ ধরনের একটি গবেষণা। কাজেই পূর্ববর্তী গবেষণার বিষয়টি যুক্তিগ্রাহ্য নয়। সংবাদপত্র বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে গবেষণা তথ্যের একটি বহুল ব্যবহৃত উৎস। শিক্ষক/গবেষকদের মধ্যে সংবাদপত্রভিত্তিক গবেষণার ব্যবহার এত ব্যাপক যে, অনেক বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে ব্যবহারকারীদের সুবিধার্থে এ সংক্রান্ত একটি webpage নিজেদের ওয়েবসাইটে দিয়ে রাখেন। সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদগুলোই এক ধরনের 'আর্কাইভাল উপাত্ত' রূপে গণ্য হওয়ার যোগ্য। সংসদের বাইরে সংসদ সদস্যদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আর কোথায় কি ধরনের সহজ অভিগম্য আর্কাইভ রয়েছে, তা বোধগম্য নয়। টিআইবির গবেষণায় শুধু সংবাদপত্রের ওপর ভিত্তি করেই করা হয়নি। দুটি সূত্র থেকে পৃথক পৃথক পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই করা হয়।
মাঠপর্যায়ে যে তথ্য সংগ্রহ করা হয় তা ছিল সংবাদপত্রে প্রকাশিত নেতিবাচক তথ্যসমূহের একধরনের যথার্থতা নিরূপণ। গুণগত গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয় তথ্যদাতাদের বা সর্বাধিক সতর্ক চয়নের ওপর। তথ্যদাতার সংখ্যা নয়, তথ্য দেওয়ার সক্ষমতাই এ ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে গণ্য। যদি সঠিক তথ্য প্রদানে সক্ষম হন তাহলে গুণগত গবেষণার জন্য একজন তথ্যদাতাও যথেষ্ট হতে পারেন। টিআইবির মাঠপর্যায়ে যারা তথ্য দিয়েছেন তথ্যদাতা হিসেবে তাদের গ্রহণযোগ্যতাও কঠোরভাবে বিবেচনায় আনা হয়। এ ক্ষেত্রে যেসব section criteria বা নির্বাচনী বৈশিষ্ট্যকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সেগুলো হলো_ ১) তথ্যদাতাদের তথ্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়ার সম্ভাবনা ২) তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে কাউকে malign তথা অযথা চরিত্রহনন না করে বস্তুনিষ্ঠভাবে তথ্য দেওয়ার প্রবণতা ৩) ধারণার বশবর্তী হয়ে 'তথ্য' প্রদান না করে প্রত্যক্ষ/পরোক্ষ অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব প্রদান এবং সর্বোপরি ৪) ব্যক্তি হিসেবে তাদের সততা। সনাকের উদ্দীপনায় সংগঠিত ৪৪টি দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের ক্ষেত্রে উপরোক্ত গুণাবলি কঠোরভাবে মেনে চলা হয়। বস্তুত তথ্যদাতারা যে কতটুকু সতর্কতার সঙ্গে তথ্য প্রদান করেছেন, সেটা একটি বিষয় থেকেই সুস্পষ্ট করা যেতে পারে। টিআইবি ২২০ জন সংসদ সদস্য সম্পর্কে তাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে যায়। কিন্তু পর্যাপ্ত তথ্য নেই বিধায় তারা মোট ৭৯ জন সম্পর্কে তথ্য প্রদান করেননি। বাকি ১৪৯ জন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল বলেই তারা তথ্য দিয়েছেন।
টিআইবি গবেষণা সম্পর্কে উত্থাপিত আরেকটি আপত্তি হলো, এটি দৈব চয়নভিত্তিক নয়। তাই এ গবেষণার ফলাফল সাধারণীকরণ করা যায় না। উল্লেখ্য, আমাদের সংসদ সদস্যদের সংখ্যা (নির্বাচিত-মনোনীত মিলিয়ে) সর্বমোট ৩৫০। এর মধ্যে ১৪৯ জন সম্পর্কে যদি তথ্য সংগ্রহ করা হয় তাহলে ওই ১৪৯ জন সব সদস্যকে বা প্রতিনিধিত্ব করার জন্য যথেষ্ট।
মাঠপর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ সম্পর্কে আরেকটি আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে, এখানে প্রশ্নগুলো ছিল গবেষণার ভাষায় যাকে বলা হয় 'leading question' অর্থাৎ ওই ধরনের প্রশ্ন যাতে গবেষকের প্রত্যাশা মতো উত্তরই উত্তরদাতা প্রদান করেন। যেমন গবেষক যদি প্রশ্ন করেন, 'আপনি কি অমুককে এবার ভোট দেবেন যদিও আপনি হয়তো জানেন, তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা হয়েছে?' এ ধরনের প্রশ্নভিত্তিক জরিপের ফলাফলে যদি দেখা যায় জনাব অমুক প্রতিপক্ষের কাছে ভোটে হেরে যাবেন তথাপি এর গবেষণাগত নিরপেক্ষতা প্রশ্নবিদ্ধ থেকে যায়। কারণ এখানে প্রশ্নের মাধ্যমে একটি উত্তর বেছে নেওয়ার জন্য উত্তরদাতাকে চালিত করা হয়েছে। টিআইবির মাঠপর্যায়ের তথ্যসংগ্রহের প্রশ্নমালা যা তথ্য মন্ত্রণালয়কে দেওয়া হয়েছে এবং যা টিআইবির ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে, সেটা যে কেউ দেখলেই বুঝতে পারবেন। এর মধ্যে এ ধরনের কোনো 'lead' প্রশ্নের অস্তিত্ব নেই। দুঃখজনক হলেও সত্য, টিআইবির গবেষণার ফলাফলকে ইতিবাচকভাবে না নিয়ে অনেকে একে নেতিবাচকভাবে দেখছেন। এর মধ্যে কাল্পনিকভাবে দেশের স্বার্থবিরোধী ষড়যন্ত্র আরোপ করা হচ্ছে। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, তার নিজ দলীয় সংসদ সদস্যদের নিজস্ব সূত্রভিত্তিক দুটি জরিপের ফলাফল তার হাতে রয়েছে। এলাকায় অনেকের পারফরম্যান্স ভালো নয়। প্রধানমন্ত্রী দলীয় সংসদ সদস্যদের এলাকায় ইতিবাচক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধির পরামর্শ দিয়ে বলেন, আরও একটি জরিপ তিনি করাবেন এবং এগুলোর ফলাফলের ওপর নির্ভর করবে কে পুনরায় নির্বাচনী টিকিট পাবে বা পাবে না। প্রধানমন্ত্রীর মতো অভিজ্ঞ ও দূরদর্শী রাজনীতিবিদ যদি মনে করেন, সংসদ সদস্যদের ইতিবাচক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধির মাধ্যমে এখনো সংশোধনের সময় আছে, তাহলে যারা বলছেন টিআইবির প্রতিবেদন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সময়ে প্রকাশ করা হয়েছে, তাদের বক্তব্যের যথার্থতা কোথায়? বরং এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, বস্তুত নির্বাচনের বিবেচনায় সঠিক সময়েই টিআইবি রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়েছে। একটি নির্বাচনী এলাকায় নির্বাচনের ফলাফল অন্যান্য উপাদানের মধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর কর্মকাণ্ড দ্বারা সৃষ্ট ইমেজের মাধ্যমেই নির্ণিত হওয়া সম্ভব বেশি। এলাকার সাধারণ ভোটার অনির্দিষ্টভাবে দেশের ১৪৯ জন সংসদ সদস্য সম্পর্কে টিআইবি কি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল তাই দেখে ভোট দেবেন এ কথা ভাবার কোনো সঙ্গত কারণ থাকতে পারে না।
এটিও দুঃখজনক যে, টিআইবির গবেষণা সংক্রান্ত আলোচনায় সংসদ সদস্যদের নেতিবাচক কর্মকাণ্ডের বিষয়টিই শুধু আলোচিত হচ্ছে। উপরে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, এ গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী সংসদ সদস্যদের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ (১৪৯ জনের মধ্যে ৫৪%) ইতিবাচক কর্মকাণ্ডে জড়িত যা প্রায় চার বছর ধরে পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদসমূহ স্ক্যান করে সেভাবে পাওয়া যায়নি। কোনো কাঠামোগত বাস্তবতার ফলে সংসদ সদস্যরা নেতিবাচক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছেন এবং কি ধরনের নীতিগত পরিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমান অবস্থার অবসান ঘটিয়ে সংসদ সদস্যদের অধিকতর গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করা যেতে পারে, এ সম্পর্কে টিআইবি গবেষণায় আলোকপাত করা হয়েছে কিন্তু এই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোই অনালোচিত রয়ে গেছে। এর মধ্যেও একটি শুভ দিক এই যে, এই প্রথম কোনো একটি গবেষণা প্রতিবেদনের পদ্ধতি সম্পর্কে সরকারের তরফ থেকে জানতে চাওয়া হয়েছে। আজ পর্যন্ত সমাজ গবেষণার নিখুঁত সর্বজনগ্রাহ্য কোনো পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়নি। সমাজ গবেষণায় পদ্ধতিগত বিতর্ক একটি চির চলমান, চির অমীমাংসিত বিষয়। তবুও বিশ্বব্যাপী দেশে দেশে অসংখ্য নীতি-নির্ধারণী গবেষণা পরিচালিত হচ্ছে। এর একাডেমিক মূল্য নিয়ে কিছু বিতর্ক থাকলেও সামাজিক নীতির পরিবর্তন সূচনায় এগুলোর ভূমিকা অনস্বীকার্য। টিআইবি মনে করে, এ দেশের গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে বর্তমান গবেষণা উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম।
লেখক : পরিচালক, গবেষণা ও পলিসি, টিআইবি
লিখাটি ২২ ডিসেম্বর, ২০১২ ![]() পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।
পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।